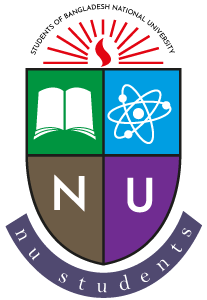ভূমিকা : দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩৯ সালে। কেউ কাউকে আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত হয় এ চুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৪১ সালে রাশিয়া আক্রমণ করে জার্মানি এই চুক্তি ভঙ্গ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা আরো ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে। এ চুক্তি দীর্ঘ কোনো সুফল দিতে পারেনি সাময়িক স্বস্তিদায়ক হলেও এ চুক্তি সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :
১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পটভূমি ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পটভূমি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :
১. রাশিয়াকে শক্তিশালীকরণ : পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো রাশিয়ার সাথে বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের পর থেকে। এছাড়া ইউরোপের অপরাপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ছিল রাশিয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ উদাসীন। হিটলার পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে পুনর্মিলনের আস্থা হারিয়ে ফেলেন ১৯৩৬ সালে হিটলার যখন মুসোলিনীর সাথে সাম্যবাদ বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তখন ফ্রান্স ও ব্রিটেন একে সমর্থন জানিয়েছে ইত্যাদি কারণে। কারণ হিটলার ১৯৩৯ সালের ২৮ এপ্রিল এক ভাষণে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তাঁর স্বাভাবিক আক্রমণ এড়িয়ে গিয়ে পশ্চিমা শক্তিবর্গ ও নাৎসি জার্মানির মধ্যে এক পক্ষকে বেছে নেবার দরকষাকষির সুযোগ নিলে অবস্থার চাপে পড়ে হিটলারকেই বেছে নেন স্ট্যালিন। হিটলারের প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলানোর চেয়ে অবশ্যম্ভাবীকে মোকাবিলা করার জন্য সময় নিয়ে রাশিয়াকে শক্তিশালী করে গড়তে হবে এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন |
২. পোল্যান্ডের আপত্তি : পোল্যান্ডের ও আপত্তি ছিল রাশিয়ার সাথে মিত্রতায়। রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনে পোল্যান্ডের অভিপ্রেত ছিল না কারণ দীর্ঘদিন রুশ প্রভাবাধীনে থাকার ফলে রাশিয়ার প্রতি পোল্যান্ডবাসীদের বিদ্বেষভাব জন্মেছিল এবং এরা এ ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকেও।
৩. জাপানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন : রাশিয়ার সাথে রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতি জার্মানি জাপানের সম্পর্ক খারাপ ছিল। রাশিয়া একই সময়ে পশ্চিমে ভাঙন মনে করে আর তাই কিছুদিনের জন্য জার্মানির সাথে চুক্তি করে হলো ও পূর্বে জাপান উভয়ের সাথে মোকাবিলা করা কঠিন। হিটল হিটলারকে শান্ত করতে চেয়েছিল। এছাড়া হিটলারের মাধ্যমে জাপানের সাথেও সম্পর্কোন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন রাশিয়া।
৪.. অনাক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করা : ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হিটল সাথে একটি ত্রিশক্তি চুক্তির প্রস্তাব করেছিল রাশিয়া ঐ সময়। পৃথিবীর যেকোনো অংশে আক্রমণাত্মক কার্যের বিরোধিতা করার যার ইউে উদ্দেশ্য ছিল । কিন্তু তাতে রাজি হয়নি ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এমতাবস্থায় । ইউে সোভিয়েত রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে একমাত্র পন্থা হিসেবে উচ্চ ধরে নিল জার্মানির সাথেই অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করা।
৫. মিউনিখের তিক্ত অভিজ্ঞতা : হিটলারকে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ তোষামোদ করে তাঁকে পূর্বদিকে আক্রমণে প্ররোচিত করবে যাতে রাশিয়া ও জার্মানি নিজেদের মধ্যে ধ্বংস যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে এবং এভাবে তারা অক্ষত থাকবে এটা স্ট্যালিন মিউনিখের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলেন। তাদেরকে এভবে প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ না দিয়ে স্ট্যালিন, বরং নিজে হিটলারের সাথে আঁতাত গড়ে তুলে বাল্টিক অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পান ।
রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রভাব বা ফলাফল : রুশ- জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সবার কাছে এই চুক্তির পরবর্তী ইতিহাস জানা আছে। এই চুক্তি হবার মাত্র ৭দিন পরেই ইউরোপের ইতিহাস দ্রুতগতিতে এগোতে থাকে এবং পোল্যান্ড আক্রমণ করে হিটলার। একটি নতুন মাইলফলক এই ইতিহাসের গতিধারায় অঙ্কিত হয় যা পরবর্তীতে | ১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয় ।
নিম্নে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রভাব/ফলাফলগুলো দেওয়া হলো :
১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা : রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট। জার্মানির অনাক্রমণ শর্ত মেনে নেয় এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যার ফলে হিটলারের পোল্যান্ডে দখলের বাধা সরে যায় এবং ৭ দিন পরে হিটলার তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পোল্যান্ড আক্রমণ করে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। পোল্যান্ড রক্ষার যে ঘোষণা ব্রিটেন ও ফ্রান্স পাঁচ মাস আগে দেয় তার ভিত্তিতে ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইতিহাসের স্মরণীয় দ্বিতীয় মহা বিশ্বযুদ্ধ এর মাধ্যমেই শুরু হয় ।
২. সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পূর্ব ইউরোপ আক্রমণ : অনাক্রমণ চুক্তির গোপন ধারাগুলো কার্যকর করার জন্য উদ্যোগী হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চুক্তি মোতাবেক পূর্ব পোল্যান্ড দখল করে নেয় ১৯৩৯ সালের শরতে। পরবর্তীতে সোভিয়েত । ফিনল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হয় ১৯৩৯ সালের ৩ নভেম্বর এবং ফিনল্যান্ডের সীমান্ত এলাকা দখল করে নেয় চার মাসের মধ্যে। তারপর সোভিয়েত গোপন ধারার শর্ত অনুযায়ী দখল করে। বাল্টিক অঞ্চল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য পূর্ব ইউরোপের বাল্টিক রাষ্ট্রে এসে উপস্থিত হয় ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মে। তারপর একের পর এক দখল করে নেয় বাল্টিক রাষ্ট্র ও রুমানিয়ার প্রদেশ বুকোভিনা এবং বেসারাবিয়া ।
৩. জার্মান দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত এবং চুক্তির ভাঙন : জার্মানি দ্বারা এই চুক্তির সম্পূর্ণ অবমাননা হওয়া এবং হিটলারের আদেশে জার্মান সৈন্যের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ হলো এই চুক্তির সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ প্রভাব বা ফলাফল ।
জার্মানি তার সামরিক ব্যক্তি দ্বারা একের পর এক সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে পরাজিত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর। হিটলারের নাৎসি বাহিনী ফ্রান্সকে পরাজিত করে ১৯৪০ সালের জুন মাসে। হিটলারের নাৎসি বাহিনী ফ্রান্সকে পরাজিত করে ইউরোপের মধ্যে। হিটলারের নাৎসি পতাকা উত্তোলিত হয়। ইউরোপের মধ্যে। তারপর পূর্ব ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে উচ্চাভিলাষী হিটলার। হিটলারের অক্ষয়শক্তিতে কিছু নতুন দেশ যোগ দেয় ১৯৪০ সালের নভেম্বরে। পূর্ব থেকেই হিটলারের সাথে যুক্ত ছিল রোমানিয়া, হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া, জাপান ও ইতালি ।
হিটলার তার সৈন্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় গোটা মধ্য ইউরোপকে পদস্থ করে। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি শেষে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায় ১৯৪১ সালের ২২ জুন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে এক শোকের অধ্যায় ছিল এটি। হিটলার এমন একটি কাজ করবে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা স্ট্যালিন বুঝতে পারেনি ।
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, কোনো সুফল বয়ে আনেনি ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। একদিকে যেমন জার্মান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ করে, তেমনি রাশিয়া পোল্যান্ড এর অনেক বড় এলাকা দখল করে নেয় এ চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় জার্মানি ১৯৪১ সালে রাশিয়া আক্রমণ করলে ।
ভূমিকা : ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ায় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। আর এই নবগঠিত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত সচেতনতার সাথে গ্রহণ করা হয়। সে সময়কার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়। সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনার করা হয়। আমরা এখানে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির তিনটি পর্যায় তুলে ধরব।
নিয়ে সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতির পর্যায়গুলো তুলে ধরা হলো : প্রথম পর্যায় : পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিরোধিতাকে প্রতিহত করতে সোভিয়েত সরকার যেসব নীতি প্রয়োগ করে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো :
প্রথমত, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালে বলশেভিক পার্টির নেতা ভি.আই. লেনিন বিশ্বযুদ্ধকে জারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। বিপ্লবের পর ক্ষমতাসীন হয়ে লেনিন ঘোষণা দেন যে, বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা তার সাম্যবাদী আদর্শের পরিপন্থি এবং রাশিয়া এ যুদ্ধে জড়িত থাকলে বলশেভিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এজন্য লেনিন ক্ষমতায় এসেই রাশিয়াকে বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরিয়ে নেয়। যুদ্ধমান দেশগুলোকে চুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের আবেদন জানায়। কিন্তু মিত্রপক্ষের কেউ এতে সাড়া দেয়নি। উপরন্তু রাশিয়ার মিত্রপক্ষ থেকে সরে যাওয়ায় মিত্রশক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ফলে এদেশগুলো মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
দ্বিতীয়ত, ১৯১৭ সালে যুদ্ধ চলার সময়ে রাশিয়ার সীমান্তে জার্মান সেনার একটি বিরাট বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ শান্তির ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। তাই নতুন সোভিয়েত জার্মানির সাথে মৈত্রী স্থাপনে উদ্যোগী হয় । বিপ্লব পরবর্তী নব গঠিত সোভিয়েত রাশিয়ার টিকে থাকার জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা জরুরি ছিল।
তৃতীয়ত, বলশেভিক সরকার যখন ক্ষমতা দখল করে, সেসময় রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ও জনবল নিয়োগের কারণে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। এমতাবস্থায় বলশেভিক সরকার জার আমলে গৃহীত সকল বৈদেশিক ঋণ ও চুক্তি অস্বীকার করে। তারা জানায় জার কর্তৃক গ্রহীত ঋণ জার পরিশোধ করবে, জনগণ নয়। এতে পশ্চিমা শক্তি তথা মিত্রপক্ষ বলশেভিক সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হয় ।
চতুর্থত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগে রাশিয়া সরকার তার আরেক উদ্দেশ্য পূরণের উদ্যোগ নেয়, আর তা হলো বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করে বিশ্বে সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। রাশিয়া তার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। ১৯১৯-২০ সালের দিকে রাশিয়ার সমর্থনে জার্মানির ব্যাভেরিয়া এবং হাঙ্গেরিতে সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটে ও পরে তা ব্যর্থ হয়। এরপর ফ্রান্স ও ব্রিটেনে বিপ্লবের চেষ্টা করেও রাশিয়া ব্যর্থ হয় ।
দ্বিতীয় পর্যায় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগে সোভিয়েত রাশিয়া নিজের অবস্থানকে শক্ত করার জন্য ইউরোপের মধ্যে তার সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করে। যার ফলে ইউরোপীয় সমগ্র শক্তি একযোগে রাশিয়ার উপর আক্রমণ চালাতে থাকে এবং সাভিয়েত সরকারকে উৎখাত করতে রাশিয়ার বিপ্লব বিরোধী বাহিনীকে সরকারের বিরুদ্ধে উস্কে দেয় । ফলে সোভিয়েত সরকার দ্বৈত সমস্যার মুখোমুখি হয়। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে অর্থাৎ পশ্চিমাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন রাশিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা ছিল পশ্চিমাদের জন্য বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। ১৯২২ সালের ১৫ এপ্রিল রাশিয়া ও জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী র্যাপেলো চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির মাধ্যমে দুই ভার্সাই চুক্তি বিরোধী শক্তি জোটবদ্ধ হয়।
বলশেভিক সরকার ঘোষণা দেয় যে রাষ্ট্র রাশিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান করবে সে রাষ্ট্রকে রাশিয়া রাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করবে। ১৯২৪ সালে নির্বাচনে জয়ী ব্রিটেনের লেবার পার্টি সোভিয়েত সরকাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর ফ্রান্স, ইতালিসহ ইউরোপের আরো ৯টি দেশ রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। শুধু যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করে। ১৯২৪ সালে লেনিন দেহত্যাগ করলে রাশিয়ার ক্ষমতায় আসেন আর এক কিংবদন্তী যোসেফ স্ট্যালিন। স্ট্যালিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রটস্কির মধ্যে সাম্যবাদ প্রয়োগ প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দেয়। এরই মধ্যে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টরা গণঅভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। সোভিয়েতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটেনের শ্রমিকরা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্রিটেনের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটে রাশিয়ার শ্রমিকদের হাত ছিল, এই অজুহাতে ব্রিটেন রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ক্রমে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের সাথেও রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
তৃতীয় পর্যায় : ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের পর সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন হয়। এই পর্যায়ে এসে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি ছিল নিজেকে রক্ষা করা। সোভিয়েত ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি সমর্থন করেনি, কারণ এর ফলে তার পশ্চিমের এলাকাগুলো সোভিয়েতের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিটলারের উত্থান, দূরপ্রাচ্য জাপানের আগ্রাসন এবং হিটলারের পূর্ব ইউরোপের দিকে অভিয়ানের ঘোষণা এসব কারণে সোভিয়েত সরকার এই সময়ে ভার্সাই চুক্তি মেনে নেয়। কারণ এই চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার উপর জার্মানির আগ্রাসন নীতি প্রতিহত করার সম্ভাবনা ছিল ।
রাশিয়া ও ফ্রান্স- এই দুই হিটলার বিরোধী রাষ্ট্র নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে ১৯৩৫ সালে একটি অনাক্রমণ চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স ও রাশিয়া তৃতীয় কোনো শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে পরস্পরের সহযোগিতা করবে প্রতিশ্রুতি দেয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সাথে রাশিয়ার সমঝোতামূলক সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সোভিয়েতের সাথে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমঝোতা সম্পর্কে অবনতি হতে থাকে। কারণ--
১. ব্রিটেনের টোরী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোর বিরোধী ছিল।
২. ভার্সাই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জার্মানি তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকলে পশ্চিমা শক্তি ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানিকে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি।
৩. ১৯৩৬ সালে হিটলারের জার্মানি ও মুসোলিনির ইতালি চুক্তির মাধ্যমে অক্ষয় শক্তি বা জোট গঠন করে। ফলে রাশিয়ার পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত হুমকির মুখে পড়ে।
৪. ১৯৩৮ সালে হিটলার অস্ট্রিয়াকে দখল করে জার্মানির সাথে যুক্ত করলেও কোনো উদ্যোগ না নিয়ে জার্মানির কোষণ করে চলছিল।
৫. জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল দাবি করে এবং যুদ্ধের হুমকি দেয়। এর ফলে ফ্রান্স-রাশিয়ার চুক্তি মোতাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার নিরাপত্তার জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথভাবে জার্মানিকে বাধা দেয়ার কথা। কিন্তু ফ্রান্স তা করতে অস্বীকৃতি জানায় ।
৬. হিটলারের আগ্রাসী কার্যক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তোষণনীতির আশ্রয় নেয়। যাতে পুরো চেকোস্লোভাকিয়াকে জার্মানি দখল করে নেয়। এর ফলে জার্মানির সীমান্ত রাশিয়ার সীমান্তের কাছে চলে আসে। অর্থাৎ রাশিয়ায় জার্মানির আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়
উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে রাশিয়া বুঝতে পারে জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো অনাগ্রহী। পুঁজিবাদী জার্মানির মাধ্যমে তারা রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চায়। যাতে রাশিয়া পশ্চিমাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার আশা ত্যাগ করে সম্পর্ক ছিন্ন করে ।
উপসংহার : পরিশেষে আলোচনা করা যায় যে, ১৯১৯-১৯৩৯ সালের পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জোট চুক্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হয়। হিটলারের উত্থানও আগ্রাসী নীতি থেকে রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমাদের সাথে জোট গঠনে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত জার্মান-রুশ অনাক্রণ চুক্তির মাধ্যমে নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সফল হয় ।
ভূমিকা : বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ১৯১৭ সালের নভেম্বরে গঠিত হয়। লেনিন ১৪টি সাম্রাজ্যবাদী দেশের জোটবদ্ধ নৃংশস আক্রমণ প্রতিহত করে। পরবর্তীতে সোভিয়েত | পালন নেতৃত্বে। নৃশংস হিটলারের অপরাজেয় নাৎসি বাহিনীকে ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠে স্ট্যালিনের স্বাধীন পরাজিত করতে সমর্থ হয় অজেয় লালফৌজ বাহিনী দুই কোটি নারীর সোভিয়েতবাসীর মৃত্যু সত্ত্বেও। স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতুনভাবে গড়ে তোলে স্ট্যালিনের পুনর্গঠনে মনোযোগী হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। ।
→ রাশিয়ার সমাজতন্ত্র সংহতকরণে যোসেফ স্ট্যালিনের সংকি কৃতিত্বসমূহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো : কৃতিত্বসমূহ : রাশিয়ার সমাজতন্ত্র সংহতকরণে যোসেফ স্ট্যালিনের
১. গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান : জনগণের কমিউনিজম শিক্ষ গড়ার সহযোগী হিসেবে ঘোষণা করা হয় কমিউনিস্ট পার্টিকে। কর সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত নাগরিকের বিস্তৃত করা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিবেকের স্বাধীনতা, | পদ বাকস্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও প্রদান করা হয় ।
২. সোভিয়েত জাতিসমূহের সমানাধিকার : সমান সমান আ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলোর স্বেচ্ছামিলনী হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর প্রজাতন্ত্র ১৯২২ সালে সোভিয়েত গঠনের সময়ে ৪টি ছিল না কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১১টি ছিল। এ কারণে প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের ক মানুষকে সমঅধিকার দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। ধারণা করা হয় লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্ট্যালিন অবশ্যই এ কাজ | - করেছিলেন । তাছাড়া বহু জাতির রাষ্ট্র হলো সোভিয়েত সংবিধানে বলা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত জাতির অধিকার সমান সমান, তারা থাকে ভ্রাতৃত্বসুলভ বন্ধুত্বের মধ্যে ।
৩. রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা : বার্ধক্য কিংবা অসুস্থতার দরুণ 1 যেসব নাগরিকের কর্মহানি ঘটবে তাদের ভরণপোষণের ভার চিকিৎসাকালীন নেবে রাষ্ট্র এ সম্পর্কে সংবিধানে বলা আছে। মজুরির ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ অবধি মজুরি লাভ করার অধিকার পায় শ্রমিকেরা। তাছাড়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে অসুস্থরা চিকিৎসা সেবা লাভ করবে।
৪. জনগণের দায়দায়িত্ব : সোভিয়েত ভূমিকে রক্ষা করার প্রত্যেকের পবিত্র কর্তব্য এটি সংবিধানে বলা হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানে বলা হয়, সোভিয়েত জনগণের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালনের কথা। আরো বলা হয়, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন মেনে চলা, দেশের সম্পদের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মানুষের মালিকানার মনোভাব, শ্রম শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং সাধারণের . সম্পত্তি বজায় রাখার কথাও।
৫.ধর্মীয় স্বাধীনতা : বলা হয়েছে নিজেদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে সকল সোভিয়েত নাগরিক। কেননা ধর্মীয়, স্বাধীনতা সংবিধানে প্রদান করা হয় ।
৬. নারীর অধিকার প্রদান : সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বক্ষেত্রেই নারীর অধিকার পুরুষের সমান এবং এটি দৃঢ়তাসহকারে সংবিধানে পুনর্ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা নারীর অধিকার প্রদানই হলো ১৯৩৬ সালের সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এ. সংবিধানে। তাই সোভিয়েতের ইতিহাসে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোর দেয়ার কারণে এ সংবিধানের গুরুত্ব অপরিহার্য
৭. শিক্ষার অধিকার : সকল সোভিয়েত নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৩৬ সালের সংবিধানে। সাধারণ শিক্ষা বিদ্যালয়, বিশেষিত মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। তাছাড়া বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাই সংবিধানে উল্লিখিত এই অধিকারটি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
৮. রিপাবলিকগুলোর স্বাধীন সৈন্য : প্রতিটি রিপাবলিককে স্বাধীন সৈন্য রাখার অনুমতি প্রদান করা হয় সংবিধানে। দেশপ্রেমী ও আত্মত্যাগী ছিলেন এ সৈন্যরা। তাই এদেরকে বলা হয় Real Army.
৯. যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার অধিকার : সকল নাগরিককে যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করা হয় ১৯৩৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী। সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকের কাজ করার অধিকারের মাধ্যমে। কাজ করার অধিকার বলতে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারদের কাজে নিয়োজিত করাকে বোঝায়। তাছাড়া কাজের পরিমাণ আর গুণের উপর মজুরি নির্ভর করে।
১০. শ্রমজীবী মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা : সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ অনুগ্রহশীল শ্রমজীবী জনগণের অবকাশ অবসরের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে। বেতনসমেত ছুটি, সুদৃঢ় বিস্তৃত জালের মতো সব বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্য নিবাস এবং কোর্ডি হাউস প্রভৃতি সংবিধানের বিশ্রাম অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মানুষ এই সব জায়গায় ছুটি কাটাতে পারে ।
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যয়, স্ট্যালিনের পুনর্গঠন নীতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত রাশিয়াকে পুনরুজ্জীবন প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ সোভিয়েতের বিভিন্ন সমস্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দেখা যায় তিনি ছিলেন জনকল্যাণকামী। ফলশ্রুতিতে সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয় তার নেতৃত্বে। এ কারণেই সাধারণ জনগণ তাদের দেশের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করে। সমগ্র বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় করে তোলে তাদের দেশপ্রেমকে ।
ভূমিকা : স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী দুই নেতা । সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছে স্ট্যালিন কিন্তু ট্রটস্কি এর বিরোধিতা করে। সবসময় সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ার বিরোধী ছিলেন ট্রটস্কি। বিভিন্নভাবে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন তিনি লেনিনের সমালোচনা করে। তাই ট্রটস্কিসহ তার সমর্থকদের দমন করে দল থেকে বহিষ্কার করেন স্ট্যালিন । স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির পরিচয় : সমর দপ্তরের কর্তা ছিলেন ট্রটস্কি। আপসহীন নীতিকে ঘৃণা করতেন তিনি। লাল ফৌজ গঠন করে প্রতি বিপ্লবীদের দমন করেন ট্রটস্কি। গোঁড়া বিপ্লবী ও তীক্ষ্ণ বৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন তিনি।
অন্যদিকে, CPSU বা রুশ কমিউনিস্ট দলের সম্পাদক এবং স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ বিভাগের কর্তা ছিলেন স্ট্যালিন। প্রভিদা পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি গৃহযুদ্ধের সময় সশস্ত্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এবং গুপ্ত পুলিশ বা চেকার প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি ছিলেন বলশেভিক দলের সেরা নেতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০৭-১৯১৭ খ্রি. মধ্যে ৭ বছর জেলেই ছিলেন তিনি । তার বিশেষ অবদান ছিল ১৯১৭ খ্রি. বলশেভিক বিপ্লবে ।
দ্বন্দ্বের সূচনা : ব্যক্তিগত সংঘাত এবং আদর্শের সংঘাত গড়ে উঠে স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে ১৯২৪ সালে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দা-কুমড়া সম্পর্ক বিদ্যমান তিনি মনে করেন। ধনতন্ত্রী দেশগুলো রুশ দেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল হতে দিবে না বলে তার ধারণা ছিল। অভ্যন্তরীণ সংগঠনের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে এজন্য তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর জোর দেন স্ট্যালিন ট্রটস্কির বক্তব্যের প্রতিবাদে এই মন্তব্য করেন।
পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে স্ট্যালিন স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেন পলিটবুরো থেকে ট্রটস্কিপন্থিদের বহিষ্কৃত করার মাধ্যমে। স্বদেশে পুঁজিতন্ত্র খতম করার মতো শক্তি সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণির ছিল না। এ সম্পর্কে ট্রটস্কি মতামত দেন । ট্রটস্কিপন্থিদের মধ্যে লেনিনবাদ বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 'নয়া প্রতিপক্ষ' মৈত্রী জোট করে। ট্রটস্কিরা সোভিয়েত অর্থনীতিকে পুঁজিতন্ত্র নাম দিয়ে বলতেন সোভিয়েত জনগণ যা গড়েছিল সেটা সমাজতন্ত্র নয় পুঁজিতন্ত্র। ট্রটস্কি সোভিয়েত ইউনিয়নের বা কোনো কঠিন সমস্যার ভাঙন ধরাবার চেষ্টায় ছিলেন।
লেনিনবাদ জলাঞ্জলি দিয়েছে তা ১৯২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে ১৫শ পার্টি কংগ্রেস থেকে বলা হয়। তারা অধঃপতিত হয়েছে। পরে ট্রটস্কিপন্থিদের এসব মিথ্যা তথ্য ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে দেশ বিদেশে নির্বাসিত হন ট্রটস্কি।
সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করার কারণ : ট্রটস্কি বলেছেন, অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী করা হলে তা হবে মার্কসবাদের বিচ্যুতি। তাই সোভিয়েত সরকারের আসল কাজ হলো বিশ্বের অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদ বা ব্যক্তিগত মূলধনকে ধ্বংস করা যা সম্পর্কে তিনি মতামত দেন। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর হস্তক্ষেপের মুখে কেবলমাত্র রুশ দেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব স্থায়ী হবে না। ট্রটস্কি মত প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্ব বিপ্লব এবং স্থায়ী বিপ্লবের কথা।
সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের দা-কুমড়া সম্পর্ক। তাই উভয়ের সহাবস্থান অসম্ভব বলে ট্রটস্কি মতামত দেন। কৃষকরা শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করবে বলে তিনি ধারণা করতেন। প্রধান প্রধান পশ্চিমী দেশ থেকে পুঁজিতন্ত্রের অবসান হওয়া অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব নয়, ট্রটস্কি পৃথকভাবে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার বিপক্ষে এ কথা বলেছেন। তার মতামত অনুযায়ী, স্বদেশে পুঁজিতন্ত্র খতম করার ক্ষমতা সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণির ছিল না। তার মতে, সোভিয়েত শ্রমিকেরা তখনই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারবে যখন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করতে পারবে।
ট্রটস্কি যেভাবে লেনিনবাদ বিরোধি ছিলেন : ট্রটস্কি তখনই পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগানোর চেষ্টা করেছে যখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো কঠিন অবস্থায় পড়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশকে নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামে। ট্রটস্কি শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর বিপণনের সমস্যার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই অভিযোগ তুলে ধরেন। পার্টি শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমানোর জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ট্রটস্কি এর বিরোধিতা করে দাম বাড়াতে চেয়েছিল। কৃষকদের অসন্তোষ এতে সৃষ্টি হবে বলে তিনি জানতেন। তাই দ্রব্যসামগ্রীর দামকে সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য পার্টি ট্রটস্কির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে পুনরায় স্বস্তি ফিরে আসে।
ট্রটস্কি যেভাবে তার মত প্রতিষ্ঠা করতে চান : বিভিন্নভাবে ট্রটস্কি তার মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। লেনিন পার্টির বিরুদ্ধে ট্রটস্কি বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং বিভিন্ন কুৎসা রটাতেন শুধুমাত্র তার মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করতেন তিনি। লেনিনের ব্যক্ত উদ্বৃত্তকে ট্রটস্কি বিকৃত করে তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলতেন শ্রমিক শ্রেণিকে। ট্রটস্কি এভাবেই তার মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হননি ।
ট্রটস্কির সহযোগী এবং পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র : লেনিনবাদী পার্টির বিরোধিতা করতেন ট্রটস্কি । সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে তাকে বাধা দিতেন। ট্রটস্কিকে লেনিন পার্টির বিরুদ্ধে প্রধান দুইজন সাহায্যকারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১. জিনোভিয়েভ, ২. কামানভ ছিলেন। ট্রটস্কি লেনিন পার্টির উপর যেকোন কঠিন অবস্থায় নতুন হামলা চালাত সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ধরাবার চেষ্টায়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছিল। এই বলে ট্রটস্কি ১৯২৩ সালে শরৎকালের শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বিপণনে সমস্যার সময় অভিযোগ তুলেন ৷ কৃষক শ্রেণির মধ্যে বিভিন্নভাবে অসন্তোষের সৃষ্টি করতেন তিনি। অক্টোবর বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে বিকৃত করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'নয়া প্রতিপক্ষ' পার্টির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আর সুবিধাবাদের অভিযোগ তুলে ট্রটস্কির অধঃপতন সাহায্যকারীরা বলেছিল পার্টি কুলাকদের অবস্থানে চলে গেছে। লেনিন পার্টি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এই দুইয়ে ভাঙনের জন্য ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ জোট ১৯২৬ সালের বসন্ত কালে অভিযান শুরু করে। ট্রটস্কি এবং তার জোট পার্টি এইভাবেই বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত থাকতো।
ট্রটস্কিপন্থিদের যেভাবে দমন করা হয় : ট্রটস্কিপন্থিরা লেনিন বিরোধী কর্মধারা প্রচারে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে লেনিনের মৃত্যুর পর থেকেই। যুদ্ধের আশঙ্কা তখন দেখা দেয় যখন ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে যায়। প্রতিপক্ষ যুদ্ধ বাধার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত সরকারকে উচ্ছেদ করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা দখল করবে বলে ট্রটস্কি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। পার্টির জন্য পিছন থেকে ছুরি মারার হুমকিস্বরূপ ছিল এই বক্তব্যটি। সোভিয়েত ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শত্রুদের সহায়তা দেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এর মাধ্যমেই।
ট্রটস্কিপন্থিরা যে ভাবধারার প্রচার করে উক্ত কারণে তাদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হবে বলে কংগ্রেস ঘোষণা দেয়। তাদেরকে অন্যান্য অনেক কমিউনিস্ট অন্তর্ভুক্ত আন্ত র্জাতিক পার্টিও বহিষ্কার করে। ট্রটস্কিপন্থিরা লেনিনবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল অত্যন্ত কলঙ্কিতভাবে সে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ট্রটস্কিকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ট্রটস্কি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চায় যদিও তিনি তেমনভাবে সফল হতে পারেনি। ট্রটস্কিপন্থিদের সকল কার্যকলাপকে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে প্রতিহত করেন স্ট্যালিন।
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ট্রটস্কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হবার পর বেশ কয়েকবার আন্দোলনের চেষ্টা করলে ও বারবার তার প্রচেষ্টা অসফল হয়। ট্রটস্কিপন্থিদের যেসব সংগ্রাম ছিল তা স্ট্যালিন প্রতিবারই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দমন করেন। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য চূড়ান্ত ক্ষমতা স্ট্যালিন অর্জন করে। নিজের অবস্থান একটি উঁচু পর্যায়ে তৈরি করতে যা তাকে পরবর্তীতে সাহায্য করেছে।
ভূমিকা : জুলিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৯১৭ সালের বা ২৫ অক্টোবর এবং গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির অনুসারে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে সংঘটিত বিপ্লবকে র বলশেভিক বিপ্লব বলা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সফল এই বিপ্লব অক্টোবর অক্টোবর বিপ্লব নামেও পরিচিত। এই বু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম কারিগররা ছিলেন মেহনতি শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষেরা। অত্যাচারী জার শাসনের বিরুদ্ধে ১৯১৭ সালে মোট ৩টি বিপ্লব সংঘটিত হয় যার সর্বশেষটি ছিল বলশেভিক নামক দলটির নেতৃত্বে দলটির নেতৃত্ব শ্রমজীবী মানুষের সাথে হাত মিলিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ে তোলে । পুঁজিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে রাশিয়াকে এক শিল্পোন্নত এবং সামাজিক সাম্যের দেশে রূপান্তরিত করে কেবল তাই নয়, বলশেভিক বিপ্লব রাশিয়া জাতিগত সমস্যারও সমাধান করেছিল। বলশেভিক বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন বিপ্লব সম্পর্কে বলেন, “যে শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা কথা বলশেভিকরা সর্বদা বলে এসেছে তা ঘটল।” বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্ম হয়।
→ বলশেভিক বিপ্লবের কারণ : নিম্নে বলশেভিক বিপ্লবের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :
১. কৃষকদের অসন্তোষ : তৎকালীন রাশিয়া ছিল কৃষিপ্ৰধান দেশ। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। তার উপর অতিরিক্ত করারোপ ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অত্যাচারে কৃষকরা নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল । ফলে তাদের ভিতরে তীব্র অসন্তোষ জমা হতে থাকে।
২. ভূমিব্যবস্থা : জার শাসনামলে রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা চালু ছিল। সমাজ ভূমিমালিক তথা জমিদার এবং ভূমিদার ই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষিজমির উপর ভূমিদাস তথা কৃষকের কোনো স্বত্ব বা মালিকানা কৃষকদের উপর অত্যাচার করতো। কখনো কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও খাজনা মওকুফ করা হতো না। ফলে এই অসম ও অন্যান্য ভূমি ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের ভূমিমালিকদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ছিল।
৩. বেকারত্ব : দুর্নীতিপরায়ণ জার শাসকের আমলে বেকারত্ব ভয়াবহ অধিকার ধারণ করেছিল। কারখানায় পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণি। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী একের পর এক নীতি গ্রহণ করতে থাকে। মুনাফা বৃদ্ধিই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে তারা শ্রমিক ছাঁটাই করা শুরু করে। যার ফলে প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এসব বেকার শ্রমিকেরা পরবর্তীতে জার পতনের জন্য আন্দোলনে যোগ দেয় ৷
৪. কোলাক ও জমিদারদের অত্যাচার : সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তৎকালীন রাশিয়ায় ভূমি মালিক ও সার্ফ অর্থাৎ ভূমিদাস এই দুই শ্রেণি অবস্থান করতো। ভূমিমালিকেরা উৎপাদিত ফসল ও খাজনা আদায়ের জন্য বিভিন্ন লোক নিয়োগ করতো। এসব মধ্যস্বত্বভোগী খোলাক ও জমিদারগণ সাধারণ কৃষকদের নানাভাবে শাসন ও শোষণ করতো এবং বিভিন্ন উপায়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য অত্যাচার করতো । ফলে কৃষকেরা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বলশেভিকের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে |
৫. জার সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি : জার সরকার ছিল রাশিয়ার সকল ক্ষমতার ও মর্যাদার উৎস এবং জার সরকার ছিল বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে যেকোনো ব্যাপারে জার বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষা করতো। এতে যদি সাধারণ কৃষক শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য অকল্যাণকর নীতি গ্রহণ করতে হতো জার সরকার তাতেও কুণ্ঠা বোধ করতো না। ফলে সাধারণ মানুষ জার সরকারের উপর ক্ষিপ্ত ছিল।
৬. দুর্নীতি : জার সরকারের প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি মহামারি আকার ধারণ করে। কেননা প্রশাসনের সকল রাজকর্মচারী জার নিজে নিয়োগ দিতো। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার চেয়ে জারের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দই মূল যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত ছিল। ফলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে প্রশাসন ছেয়ে যায়। পরবর্তীতে এসব রাজকর্মচারীর দ্বারা জনগণের কল্যাণসাধন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
৭. জারের দমননীতি : জনবিচ্ছিন্ন জার সরকার নিজের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সর্বদা দমননীতি পালন করতো। জার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য জনগণকে সচেতন করতে অনেক গুপ্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। পরবর্তীতে এসব গুপ্ত সংগঠনকে দমন করতে জার সরকার দমনপীড়ন নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম একটি "Union of Pablic Good" নামে গুপ্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা পায়। যারাই জার সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই দমন করা হয়েছে।
৮. পুঁজিবাদের উন্মেষ : যদিও তৎকালীন রাশিয়ার সামন্ত তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তবে তখন পুঁজিবাদেরও বিকাশ ঘটেছিল। প্রায় অধিকাংশ কলকারখানায় মালিক ছিল এসব বুর্জোয়া শ্রেণির পুঁজিপতিরা সমাজের সকল উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদকের উপায়ের মালিকও ছিল এসব পুঁজিবাদিরা। ফলে সমাজের পুঁজি একটি নির্দিষ্ট মানুষের হাতে কুক্ষিগত ছিল এবং আরেকটি বিশাল সম্প্রদায় জীবনধারণের জন্য শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য ছিল। শ্রমিক শ্রেণিকে ইচ্ছামতো শোষণ করা হতো। ফলে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠে|
বলশেভিক বিপ্লবের ফলাফল : বলশেভিক বিপ্লব মানব ইতিহাসের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই এর ফলাফলগুলোও ছিল তেমনই যুগান্তকারী।
৯. সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র : বলশেভিক বিপ্লবের সবচেয়ে বড় ফলাফল সামন্ততান্ত্রিক জার সরকার এবং বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদের পতন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে রাশিয়ার রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। পুরোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে ফেলে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় । জার শাসনামলের গঠিত সিনেট ভেঙে দেয়া হয় ।
১০. নতুন অর্থব্যবস্থা : সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদকের উপায় সবকিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে যাওয়া হয়, এমনকি বণ্টন ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিপ্লবের পরে সকল কলকারখানা ও ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানার চলে যাওয়ার বুর্জোয়া শ্রেণির অবসান ঘটে। শ্রমিকের মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শোষণের পথও বন্ধ হয়ে যায় ।
১১. নতুন শাসনতন্ত্র : বিপ্লবের ফলে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করা হয়। রাশিয়ার ডুমা বা সংসদকে ভেঙে ফেলা হয়। রাশিয়ার যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান বলশেভিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল নতুন সরকার এসে সেগুলো ভেঙে দেয়। জার শাসনামলের সিনেট ভেঙে দেয়। জার প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি সেনাবাহিনীতেও অনেক সংস্কার করা হয় ।
১২. বলশেভিক দলের ক্ষমতা গ্রহণ : অক্টোবর বিপ্লব বলশেভিক দলের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। দলটির নেতৃত্বে তৎকালীন রাশিয়ার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সকল সাধারণ মানুষ বিপ্লবে অংশ নেয় । ফলে প্রশাসনের শূন্যতা পূরণ করতে বলশেভিক দলটি ক্ষমতায় আসীন হয় । নবপ্রতিষ্ঠিত দলটির নেতৃত্ব ছিলেন ট্রটস্কি এবং লেনিন। তাদের হাত ধরে পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয় ।
১৩. নতুন পররাষ্ট্রনীতি : বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে আমূলে পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে রাশিয়া পোল্যান্ডের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে রাশিয়ার লালফৌজ এই যুদ্ধে সফলতা লাভ করলেও আন্তর্জাতিক নীতির কারণে কার্জন লাইন বরাবর যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা মেনে নিতে বাধ্য হয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তুরস্কের সাথে আক্রমণ চুক্তি করে রাশিয়া ।
১৪. ধর্মনিরপেক্ষতা : সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর বলশেভিক সরকার অনেকগুলো ধর্মীয় সংস্কার সাধন করে। গির্জাকে রাষ্ট্রে থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। গির্জার অন্তর্গত সকল জমি রাষ্ট্রের মালিকানায় নেয়া হয়। নাগরিকের বিয়ে ও তালাকের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেয়া হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতামূলক রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় ৷
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে জার সরকারের শোষণের অবসান ঘটে নতুন এক রাশিয়ার জন্ম হয়। কার্ল মার্কসের দর্শনে উদ্বুদ্ধ লেনিন এক শোষণহীন ও সামাজিক ন্যায্যতা ও সমতার জন্য সমাজ গঠনে সামনে এগিয়ে যায় এবং লেনিন সমাজতন্ত্রের সকল নীতিকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সবকিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্ত র্ভুক্ত করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়া জারতন্ত্র থেকে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। তিনি পরে নতুন শাসনতন্ত্র প্রদান করেন এবং বলশেভিক দলের নিজস্ব কর্মপন্থা ও দর্শন অনুযায়ী, সকল মানুষের মধ্যে সমতা স্থাপন, সকল জমি ও মূলধন রাষ্ট্রীয়করণ করে মানুষের জীবনের উন্নতি সাধন করেন।
ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে ৫টি পরাশক্তির অন্যতম একটি হলো রাশিয়া। একবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যেটি সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত ছিল। রাশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্রাট প্রথা চালু ছিল যাদেরকে জার বলা হতো। জারদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ আন্দোলন শুরু করে। যা পরিবর্তীতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে এবং জার প্রথার বিলুপ্তি স্বাধিত হয় ।
রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহ : সম্রাট বা জারদের অত্যাচার ও নির্যাতনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। জনগণ জারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তাদের আন্দোলনে সকল জনগণ একাত্মতা ঘোষণা করলে আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ লাভ করে। নিম্নে বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলো তুলে ধরা হলো :
১. নিহিলিস্ট আন্দোলন : জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যখন রাশিয়াতে শাসনব্যবস্থা সংস্কার সাধন করেন। তখন নানারকম নৈরাজ্য দেখা দেয় সাধারণ মানুষের উপর অভিজাতদের আধিপত্য ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সমাজে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পশ্চিম ইউরোপের মতো রাশিয়াতেও জাতীয়তাবাদ এবং মানবতাবাদের সূচনা হয় সাহিত্য সংস্কৃতি মাধ্যমে। ফলে জনগণ এই মানবতা বাদে উজ্জীবিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে যা নিহিলিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত।
২. নিহিলিস্ট ধারণার উদ্ভব : জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যখন তার শাসনব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন যেটি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বাস্তবায়ন হয়। এতে জনগণের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৮ সালে Bell নামক এর পত্রিকায় হার্জেন নামক এক ব্যক্তি এই সংস্কারের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেন। এতে রাশিয়ার ছাত্র সমাজ সচেতন হয়ে উঠে। এরপর ১৮৬১ সালে পিসারেভ তুর্গেনিভ তাঁর Father and son উপন্যাসে নিহিলিস্ট শব্দটি ব্যবহার করেন। যেটি পরবর্তী সময়ে রুশ বিপ্লবিরা তাদের আন্দোলনে নামকরণ করেন।
৩. সামাজিক বৈষম্যের প্রচার : ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক বৈষম্য ছিল। সেখানে সকল মানুষ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। একটি শ্রেণিকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় যেটি অভিজাত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত ছিল। অপরদিকে আরেকটি শ্রেণিকে সকল ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় যেটি ভূমিদাস নামে পরিচিত ছিল। এর ফলে চরম বৈষম্য দেখা দেয়। এই বৈষম্য আন্দোলনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় ।
৪. অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রচার : রাশিয়ার মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল দরিদ্র কৃষক বা ভূমিদাস। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ভূমি মালিকগণ ফসলে আবাদ করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কৃষকদের উপর কর হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করতো। ফলে কৃষকগণ আরো দরিদ্র হয়ে পড়তো। আন্দোলনে তার দরিদ্রতার কথা প্রচার করতো।
৫. নবচেতনার ডাক : রাশিয়ার অধিকাংশ জনগণ পুরাতন জার শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তরুণ উদীয়মান যুবকগণ। যারা তাদের আদর্শ হিসেবে কর্নিসেভস্কি, আলেকজান্ডার হার্জেন, বেলিনস্কি ও মাইকেল বাকুলিনকে গ্রহণ করেন। তারা বিজ্ঞান, বস্তুবাদ এবং যুক্তিবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন এবং শোষণহীন সমাজ গঠনে প্রত্যয়ী হয়ে উঠেন।
৬. নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন : রাশিয়ার আন্দোলনসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি আন্দোলন হলো নৈরাজ্যবাদ আন্দোলন। এটিকে শূন্যবাদের আন্দোলনও বলা হয়। মাইকেল বাকুনিন ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবক্তা। এই আন্দোলনের মূলকথা ছিল রাশিয়ার পূববর্তী শাসনব্যবস্থা ছিল অকল্যাণকর এবং শূন্য থেকে পুনরায় আন্দোলনের মাধ্যমে কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। যার মাধ্যমে সকল প্রকার নৈরাজ্যের বিলোপ সাধন হবে।
৭. বাকুনিন : রাশিয়ায় যাদের লেখনী বা বক্তিতার মাধ্যমে আন্দোলন সূচনা এবং পরিচালনা হতো তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন বাবুনিন। তিনি কার্ল মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে তিনি মার্কসবাদের সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। শূন্যবাদের ধারণার মাধ্যমে তিনি আলোচিত হয়ে উঠেন |
৮. নারোদনিক আন্দোলন : নারোদনিক আন্দোলন রাশিয়ার অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সময় ঘটেছিল। এটিকে নিহিলিস্ট আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় হিসেবে ধরা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বলে এটিকে নারোদনিক আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :
(ক) নারোদনিক প্রথম আন্দোলন : প্রথম নারোদনিক আন্দোলন শুরু হয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মাধ্যমে। জনগণ স্বেচ্ছায় এই আন্দোলন করেছিল বিধায় এই আন্দোলনকে People will আন্দোলন বলা হয় । প্রথমে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের রূপ নেয় ।
(খ) দ্বিতীয় নারোদনিক আন্দোলন : দ্বিতীয় নারোদনিক আন্দোলনটি ছিল মূলত কৃষ্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। প্রথম নারোদনিক আন্দোলন থেকে কৃষ্ণ বর্ণগোষ্ঠীরা আলাদা হয়ে গিয়ে পৃথকভাবে আন্দোলন শুরু করে। এদের আন্দোলন Black partition হিসেবে পরিচিত লাভ করে।
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, রাশিয়ায় যতগুলো বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার মূল কারণ ছিল সাধারণ মানুষকে সুবিধাবঞ্চিত করে রাখার ফল। মানুষ অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন শুরু করে যেটি পরবর্তীতে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে। রাশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক উন্নতির জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।
ভূমিকা: সোভিয়েত জনগণের অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন মূলগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল ১৯৩৬ সাল থেকে। তখন দেশে আর কোনো উৎপীড়নকারী ছিল না। এমন কেউ আর ছিল না যে অপরের ক্ষতি করে জীবনযাত্রা চালায়। এ সোভিয়েতে কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক নতুন সমাজ তৈরি হলো। তাই একটি পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে উঠল । আর ১৯৩৬ সালের সংবিধানে এ পরিবর্তনের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটল। স্ট্যালিন সংবিধান (Satlin constitution) হিসেবে পরিচিত ১৯৩৬ সালের সোভিয়েত সংবিধান। এ সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসরত সকল জনগণের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছিল। এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো :
১৯৩৬ সালের সংবিধান : নতুন সংবিধান রচনার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে। সংবাদপত্রে এ সংবিধানের খসড়াসমূহ প্রকাশিত হয়। এ সংবিধানের উপর সাড়ে পাঁচ মাস যাবৎ বিভিন্ন আলোচনা চলতে থাকে। এতে অংশগ্রহণ করে প্রায় ৫ কোটি জনগণ। ইতিহাসে কোন দেশের বুনিয়াদি সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে জনগণের বিরাট অংশের এমন বিস্তৃত অংশগ্রহণের ঘটনা নজিরবিহীন ছিল। এ সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৩৬ সালের ৫ ডিসেম্বর জয়যুক্ত হওয়ার পর।
এ সংবিধানের মূল বিষয়সমূহ নিচে বিশ্লেষণ করা হলো :
১. গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান : জনগণের কমিউনিজম গড়ার সহযোগী হিসেবে ঘোষণা করা হয় কমিউনিস্ট পার্টিকে। সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত নাগরিকের বিস্তৃত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিবেকের স্বাধীনতা স্বাধীনতাও প্রদান করা হয় বাকস্বাধীনতা সভা সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের |
২. সোভিয়েত জাতিসমূহের সমানাধিকার : সমান সমান ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলোর স্বেচ্ছামিলনী হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর প্রজাতন্ত্র ১৯২২ সালে সোভিয়েত গঠনের সময়ে ৪টি ছিল কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১১টি ছিল। এ কারণে প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের মানুষকে সমঅধিকার দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। ধারণা করা হয় লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্ট্যালিন অবশ্যই এ কাজ করেছিলেন। তাছাড়া বহু জাতির রাষ্ট্র হলো সোভিয়েত সংবিধানে বলা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত জাতির অধিকার সমান সমান তারা থাকে ভ্রাতৃত্বসুলভ বন্ধুত্বের মধ্যে ।
৩. জনগণের দায়-দায়িত্ব : সোভিয়েত ভূমিকে রক্ষা করা প্রত্যেকের পবিত্র কর্তব্য এটি সংবিধানে বলা হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানে বলা হয় সোভিয়েত জনগণের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালনের কথা। আরো বলা হয় রাষ্ট্রীয় আইনকানুন মেনে চলা। দেশের সম্পদের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মানুষের মালিকানার মনোভাব শ্রম শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং সাধারণের সম্পত্তি বজায় রাখার কথাও ।
৪. জনগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী : জনগণকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সোভিয়েত সংবিধানে ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েত জনগণ এতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে। শ্রমজীবী সোভিয়েত জনপ্রতিনিধি সৃষ্টি করা হয় প্রত্যেকটি গ্রামে শহরে এবং ইউনিয়নে। তাদের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলোর সমস্যা সমাধান করবে এরা এবং সরকারকে সমস্যাগুলোর কথা জানাবে।
৫. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা : সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় ১৯৩৬ সালের সংবিধানে উল্লেখ করা হয় শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশের একমাত্র মালিক হলো শ্রমিক এবং কৃষকরা। এটি সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদ উল্লিখিত।
৬. রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা : বার্ধক্য কিংবা অসুস্থতার দরুণ যেসব নাগরিকের কর্মহানি ঘটবে তাদের ভরণপোষণের ভার নেবে রাষ্ট্র এ সম্পর্কে সংবিধানে বলা আছে। চিকিৎসাকালীন মজুরির ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ অবাধ মজুরি লাভ করার অধিকার পায় শ্রমিকেরা। তাছাড়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে অসুস্থরা চিকিৎসা সেবা লাভ করবে।
৭. ধর্মীয় স্বাধীনতা : বলা হয়েছে নিজেদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে সোভিয়েত নাগরিক। কেননা ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবিধানে প্রদান করা হয় ।
৮. নারীর অধিকার প্রদান : সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বক্ষেত্রেই নারীর অধিকার পুরুষের সমান এবং এটি দৃঢ়তাসহকারে সংবিধানে পুনর্ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা নারীর অধিকার প্রদানই হলো ১৯৩৬ সালের সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এ সংবিধানে। তাই সোভিয়েতকে ইতিহাসে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জোর দেয়ার কারণে এ সংবিধানের গুরুত্ব অপরিহার্য।
৯. শিক্ষার অধিকার : সকল সোভিয়েত নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৩৬ সালের সংবিধানে। সাধারণ শিক্ষা বিদ্যালয়, বিশেষিত মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। তাছাড়া বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাই সংবিধানে উল্লিখিত এই অধিকারটি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ।
১০. রিপাবলিকগুলোর স্বাধীন সৈন্য : প্রতিটি রিপাবলিকাকে স্বাধীন সৈন্য রাখার অনুমতি প্রদান করা হয় সংবিধানে। দেশপ্রেমী ও আত্মত্যাগী ছিলেন এ সৈন্যরা। তাই এদেরকে বলা হয় Real Army.
১১. যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার অধিকার : সকল নাগরিককে যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করা হয় ১৯৩৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী। সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকের কাজ করার মাধ্যমে। কাজ করার অধিকার বলতে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারদের কাজে নিয়োজিত করাকে বোঝায়। তাছাড়া 'কাজের পরিমাণ আর গুণের উপর মজুরি নির্ভর করে।
১২. শ্রমজীবী মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা : সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষ অনুগ্রহশীল শ্রমজীবী জনগণের অবকাশ অবসরের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে। বেতন সমেত ছুটি, সুদূর ত জাতের মত সব বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্য নিবাস এবং কোডিং হাউস প্রভৃতি সংবিধানের বিশ্রাম অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মানুষ এই সব জায়গায় ছুটি কাটাতে পারে।
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, পৃথিবীতে সামন্ততান্ত্রিক দেশ হিসেবে সোভিয়েত স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৩৬ সালের সংবিধানের মধ্য দিয়ে। সাধারণ জনগণের চাওয়া পাওয়াকে গুরুত্ব প্রদান করে এ সংবিধান। সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। সোভিয়েত জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এ সংবিধান। এ কারণেই সাধারণ জনগণ তাদের দেশের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করে। সমগ্র বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় করে তোলে তাদের দেশপ্রেমকে ।
ভূমিকা : যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বা War communism নামে অভিহিত করা হয়। ১৯১৮-১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলশেভিক সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে। গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েত সরকার বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হন ১৯১৮ খ্রি. বসন্তকালে লেনিনের রচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ চালু করা হয় সোভিয়েত ও রাশিয়া গৃহযুদ্ধের সময় ।
যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ : রাশিয়ার অভ্যন্তরে অক্টোবর বিপ্লবের কিছুদিনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি হয় প্রতিবিপ্লবী শক্তি ও বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের ফলে। দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় আসে এবং জনজীবনে বিপর্যস্ত হয় ৷
শ্রমিক, কৃষকসহ দেশপ্রেমিক জনতা ও রেড আর্মি রুখে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবী শক্তি ও বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য । এমন পরিস্থিতিতে লেনিন গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য পূর্বের অর্থনৈত্বিক পরিকল্পনার পরিবর্তে দেশের অর্থনৈতিক শিল্পব্যবস্থা সবকিছু নতুন করে দাঁড় করান সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বলতে বোজায় লেনিন যুদ্ধকালীন যে অর্থনৈতিক নীতি চালু করেন তাকে ।
সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, সকল প্রকার ভূ-সম্পত্তি, শিল্প, শিল্প কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ নীতি গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় War communism বা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ হলো এ নীতির নাম। এটি একটি সামরিক ব্যবস্থা ছিল লেনিন এর মতামত অনুযায়ী ।
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে “যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ” বা “সামরিক সাম্যবাদ” চালু করা হয় সোভিয়েত রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় ১৯১৮ থেকে ১৯২১ খ্রি. পর্যন্ত। বলশেভিক শাসকগোষ্ঠী শহরসমূহের অধিবাসী এবং রেড আর্মীর অস্ত্র সরঞ্জাম ও খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে “যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ” নীতি তখন গ্রহণ করে যখন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সকল স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও সম্পর্ক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যা সোভিয়েত ইতিহাসতত্ত্ব অনুযায়ী জানা যায়। ১৯১৮ খ্রি. জুন মাসে “যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ” বলবৎ করে। ভেসেন ভেসেন খাঁ (Vesenkha) নামে পরিচিত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ। নতুন অর্থনৈতিক নীতি' (NEP) চালুর সাথে সাথে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের অরসান ঘটে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ।
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, লেনিন এক নতুন অর্থনৈতিক নীতি গড়ে তোলেন তখনই রাশিয়ার জনগণ যখন প্রতিবিপ্লবী শক্তি ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সচেতন হয় একেই বলা হয় যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ। এটি যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ নামে পরিচিতি লাভ করার কারণ ছিল এই অর্থনৈতিক নীতি যুদ্ধ চলাকালনি সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল।
ভূমিকা : যে সকল ব্যবস্থা নতুন অর্থনৈতিক নীতির অধীনে নেয়া হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ফলে সাফল্য অর্জিত হয়। রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সফলতা অর্জন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধজনিত ভয়ানক অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে নতুন অর্থনৈতিক নীতি ।
নতুন অর্থনৈতিক নীতির ফলাফল : রাশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয় ১৯২৫ সাল নাগাদ লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবে। কৃষি এবং শিল্পের উৎপাদন ১৯১৩ সালের উৎপাদন পর্যায়ে পৌঁছে ১৯২৭-২৮ সাল নাগাদ ।
শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের জন্য কৃষকরা তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারে বিক্রয় করে। এভাবে গ্রাম আর শহরের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপন হয় । শ্রমিক আর কৃষকের মধ্যে আরো জোরদার হয় মৈত্রী জোট। অপরদিকে, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া রাশিয়া উন্নতি লাভ করে রেলপথ, জল, পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে।
পুঁজিপতি ও ভূ-স্বামীদের নতুন অর্থনৈতিক নীতির কলে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল এ সকল প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে সাময়িককালের জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধাচারণ থেকে দূরে রাখা। তাদেরকে পরবর্তী সময়ে শ্রমিক ও কৃষকদের একত্র করে চূড়ান্তভাবে নির্মূল করা হয়।
এই নীতির সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুদৃঢ়করণের পথ প্রশস্ত করেছিল রাজনৈতিক দিক থেকে। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল এ উদ্দেশ্যে। নতুন অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনের নীতি সূচনা করেছিল সামাজিক ক্ষেত্রে ও। ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূমির উপর বাড়িয়ে দেওয়া হয় ফসল উৎপাদন। যার ফলে তারা পরিণত হয় বিত্তশালী কৃষকে ।
কুলাকরা ক্রমে ধ্বংস হয়ে যায় গ্রাম অঞ্চলের। একতা স্থাপিত হয় ক্ষুদ্র কৃষক, শ্রমিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মধ্যে। এছাড়া ক্ষমতার পালাবদলের প্রক্রিয়া শুরু হয় সামাজিক ক্ষেত্রেও। পররাষ্ট্রনীতিতে ও প্রতিফলিত হয় এই নীতির প্রভাব। রাশিয়ার কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটে নতুন অর্থনৈতিক নীতির কারণে। রাশিয়াকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালিসহ ইউরোপের অনেক পুঁজিবাদী দেশ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করে ১৯২৪ সালের দিকে। রাশিয়ার পুঁজি বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসে ব্রিটেনসহ অনেক দেশ।
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, মহামতি লেনিনের মহাপ্রতিভা এবং বিজ্ঞানসম্মত দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য নতুন অর্থনৈতিক নীতি। রাশিয়ার সমাজব্যবস্থাতে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয় এই নীতির ফলে। নতুন অর্থনৈতিক নীতির গুরুত্ব সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অপরিসীম।
ভূমিকা : রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম মহানায়ক হলো লেনিন। তার নেতৃত্বেই রাশিয়ার সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম ভিত্তি ছিল 'এপ্রিল থিসিস'। ১৯১৭ সালের ৪ এপ্রিল লেনিন এই বিখ্যাত থিসিসটি জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। আর এই এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমেই তৎকালীন বলশেভিক দল বিপ্লব সংক্রান্ত সকল করণীয় ও দিক- নির্দেশনা খুঁজে পেয়েছিল। কারণ এপ্রিল থিসিস ছিল লেনিনের বিপ্লবকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনার। এটি ছিল রুশদের জন্য একটি চরম পত্র যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ মুক্তির পথ নির্দেশিকা খুঁজে পেয়েছিল। এপ্রিল থিসিস প্রকাশ করার পর লেনিনের অনুসারীও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল । যার ফলে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।
এপ্রিল থিসিস : ১৯১৭ সালের এপ্রিলে বলশেভিকদের এক সভার লেনিন পার্টির নেতাদের উপস্থিতিতে একটি থিসিস পেশ করেন। এ থিসিসকে এপ্রিল থিসিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ৷ পেট্রোগ্রাদের তোরিদা কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হলেও এর তিন দিন পর প্রাভদা সভার এটি প্রকাশিত হয়। মূলত এপ্রিল থিসিসটি ছিল দলের সাধারণ কর্মীদের প্রতি একটি দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য যার মাধ্যমে সবাই বিপ্লবের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।
→ এপ্রিল থিসিসের মূল বক্তব্য : লেনিন কর্তৃক প্রদত্ত এপ্রিল থিসিসের প্রধান দিকগুলো এখানে আলোচনা করা হলো :
১. বিপ্লবের প্রথম পর্ব : লেনিন তার থিসিসের মধ্যে বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি এটা বলেও সতর্ক করেন যে প্রথম পর্বে প্রলেতারিয়েতদের জন্য কোনো স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হবে না। প্রলেতারিয়েতদের কোনো প্রতিষ্ঠানিক সংগঠন না থাকায় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা চলে গিয়েছে। বিপ্লব সফল করার জন্য প্রলেতারিয়েতদের একতাবদ্ধ হতে হবে।
২. বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব : বিপ্লবের প্রথম পর্ব বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। যার ফলে বিপ্লবের সকল রকম সুবিধা নেয়া শুরু করে। ফলে প্রলেতারিয়েতদের জন্য বিপ্লব এক প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন এ পর্বে কৃষক শ্রমিক ও মিত্র প্রলেতারিয়েতদের হাতে ক্ষমতা আসতে হবে। যাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফল মজলুম জনগণ পেতে পারে ।
৩. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া : ১ম বিপ্লবের পর রাশিয়ার সংসদীয় পদ্ধতির অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। লেনিন তার এপ্রিল থিসিসে যুক্তি দিয়ে এটা প্রমাণ করতে চলে যে, প্রথম বিপ্লবের পরে সংসদীয় পদ্ধতির অস্থায়ী সরকার থেকে সোভিয়েত এর ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে।
৪. সংসদীয় প্রজাতন্ত্রে নিষ্প্রয়োজন : লেনিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা। কেননা একমাত্র সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজে ন্যায় ও সাম্যতা প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব। আর তাই বলশেভিক পার্টি কোনো প্রকারে বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিক সরকারকে বিশ্বাস করতে পারে না। কেননা এসব পদ্ধতিতে সরকার করতে পারে না। কেননা পদ্ধতিতে সরকার প্রলেতারিয়েত শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করে না। তাই সংসদীয় প্রজাতন্ত্র সমাজের জন্য নিষ্প্রয়োজন ।
৫. তাৎক্ষণিক সরকার উচ্ছেদ করা যাবে না : ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর গঠিত সংসদীয় পদ্ধতির বুর্জোয়া সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতি ছিল সবাই। কিন্তু লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারকে উচ্ছেদ করতে গেলে কেবল রক্তক্ষয়ই হবে, এছাড়া কোনো লাভ হবে না। তাই থিসিসের এই পর্যায়ে এসে লেনিন বলেন, একটি ক্ষমতাসীন সরকারকে তাৎক্ষণিক উচ্ছেদের চিন্তা করা সহজ নয়, আর বুর্জোয়া সরকার সাময়িক বাহিনীর সহায়তার ক্ষমতায় এসেছে এটাও মাথায় রাখা দরকার।
৬. জনসচেতনতা তৈরি করা : লেনিন মনে করতেন বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদ করতে চাওয়ার চেয়ে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতনর করে তোলা উচিত। কেননা এতে দীর্ঘমেয়াদি লাভ হবে। কারণ ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের পর ক্ষমতায় বসা সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা আছে এমনকি কৃষক শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত সোভিয়েতগুলো ও বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন জানাচ্ছে।
৭. চূড়ান্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা : যেকোনো বিপ্লব শুরু করার জন্য প্রথমে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর গঠিত বুর্জোয়া সরকারের প্রতি সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আস্থা ছিল এবং সোভিয়েতগুলোর সমর্থন ছিল তখন বিপ্লব করার চেয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করাই উত্তম হবে। তাই লেনিন বলেন, একটি বুর্জোয়া বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়। সুতরাং সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা থাকা পর্যন্ত বিপ্লব সংঘটিত হবে না, বরং অপেক্ষা করতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে হবে। আর এভাবে চূড়ান্ত মুহূর্তে বিপ্লব শুরু করতে হবে।
৮. শান্তিচুক্তি : যেকোনো বিপ্লবের পরেই প্রতিবিপ্লবীদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধের কারণে যুদ্ধের প্রথম দশ মাসিইে রাশিয়ার প্রতি মাসে গড়ে তিন লাখ সৈনিক নিহত, আহত বা বন্দি হয়। ১৯১৭ পর্যন্ত রাশিয়ার গড় মাসিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল মৃত ৪০,০০০ আহত ১,২০,০০০ এবং বন্দি বা নিখোঁজ ছিল ৬০,০০০। তাই রুশ সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং দেশের ভিতরে কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে তাই যুদ্ধ থামানোর ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই লেনিন তার থিসিসে উল্লেখ করেন যে, সোভিয়েতগুলো যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিচুক্তি করা হবে।
৯. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : লেনিন তার এপ্রিল থিসিসে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ফলে সকল জমি এবং কলকারখানাগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়া হবে। অর্থাৎ সকল ধরনের উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদনের উপায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হবে এবং বণ্টন ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে নেয়া হবে। যাতে সমাজের কোনো বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব না থাকে ।
→ এপ্রিল থিসিসের গুরুত্ব : ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় লেনিন দেশে ছিলেন না। এপ্রিল মাসে দেশে ফিরে তিনি এই থিসিসটি দেন যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।
১. বিপ্লবের পথনির্দেশনা : লেনিন যেহেতু ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের সময় দেশে ছিলেন না এবং বিপ্লবের পর একটি অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা গঠিত সরকার ক্ষমতায় আসীন হয় যারা সাধারণ মানুষ নয়; বরং বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করা শুরু করে তাই লেনিন এপ্রিল থিসিসটি প্রদান করেন। যাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দল দিক-নির্দেশনা পায়। এবং এর মাধ্যমেই পরবর্তীতে বলশেভিক বিপ্লব সাধন করা হয়।
২. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার : বলশেভিক বিপ্লবে পূর্বে রাশিয়া ভাষা, ধর্ম, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে চরম বৈষম্য করা হতো। রুশভাষীরা অরুশভাষীদেরকে অবজ্ঞা করতো। তাই লেনিন ঘোষণা দেন যে, এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে সবাইকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সুযোগ দেয়া হবে। কাউকে ভাষা বা ধর্মের জন্য বৈষম্য করা হবে না এবং সব মানুষ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।
৩. শ্রমিকদের একতা : জার শাসনামলে কৃষক-শ্রমিকদের। কোনো মূল্যেই দেয়া হতো না। তার উপর তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার করা হতো। যার ফলে এক সময় কৃষক ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু তারা কেউই এক্যবদ্ধ ছিলেন না। ফলে তাদের আন্দোলন ও ফলপ্রসূ ছিল। না। এই কারণে লেনিন তার এপ্রিল থিসিসে বার বার কৃষক শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে জোর দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়।
৪. বুর্জোয়াদের পতন : লেনিনের এপ্রিল থিসিসের অন্যতম গুরুত্ব ছিল বুর্জোয়াদের পতনের জন্য। কেননা সবার উদ্দেশ্য ছিল জার শাসনামলের পতন ঘটিয়ে গণমানুষের মুক্তি ঘটবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর জার শাসনামলের অবসান ঘটেছিল বটে কিন্তু বুর্জোয়া ও অভিজাতরাই সরকার গঠন করে। যদিও সেই সরকার গণতন্ত্রপন্থি ছিল কিন্তু তাদের দ্বারা সাধারণ কৃষক শ্রমিকদের কষ্ট অনুধারণ করা সম্ভব না, বরং এতে আরেকটি শোষণের পথই চালু হয়েছে। তাই তিনি এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের পতনের ঘোষণা দেন।
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন ১৯১৭ সালের ৪ এপ্রিল থিসিস প্রদান করেন যা ছিল মূলত বলশেভিক একটি রূপরেখা ছিল। এই রূপরেখার কারণেই পরবর্তীতে একটি সফল বিপ্লব সংঘটিত হয়। যখন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক ধরনের নেতৃত্বহীনতায় ভুগছিল সেই মুহূর্তে লেনিন দিক-নিদের্শনামূলক এপ্রিল থিসিসটি প্রদান করেন। তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটানো এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করা। এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে তিনি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান এবং অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটান।